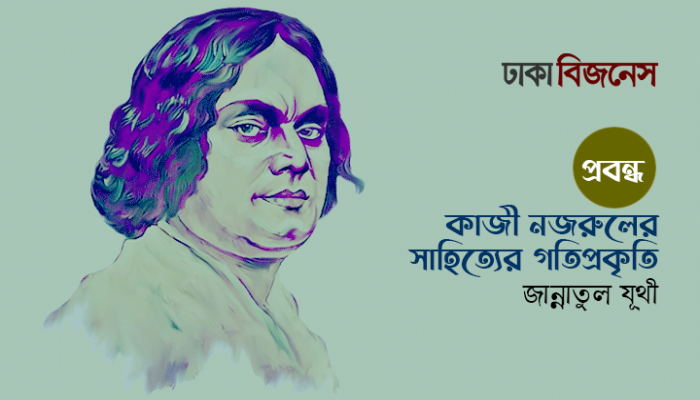
কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বহুমাত্রিক লেখক। বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের মাত্র তেইশ বছর সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। তাতেই এতো বিচিত্র-বিস্ময়! তাঁর অদম্য মেধা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম করে তুলেছে অনায়সে। উপন্যাস-গল্প-কবিতা-নাটক-অনুবাদ-প্রবন্ধ-সঙ্গীত রচনা-সম্পাদক সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর সদর্প বিচরণ। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তাঁর জীবন কেটেছে মূক হিসেবে। পিতৃ-মাতৃহীন সংগ্রামশীল নজরুল, কথা বলতে না পারা নজরুল এবং প্রমীলাহীন নজরুলের জীবন কখনোই মসৃণ ছিল না। শেষতক ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পান। তারপর ১৯৭৬ সালে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।
আমরা জানি, সাহিত্যের অন্যতম আধুনিক সৃষ্টি উপন্যাস। এই শাখায় কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্বল্পতার ভেতর দিয়েও কিভাবে সাড়া জাগানো যায় তা তাঁর উপন্যাসসৃষ্টির দিকে নজর দিলে সহজেই বোধগম্য। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন। বাঁধন-হারা ( ১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)। বাঁধন হারা কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস। তিনি যখন করাচিতে থাকতেন তখন এই উপন্যাস রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। এটি মূলত একটি পত্রোপন্যাস। বাঁধন হারা'র প্রথম কিস্তি মোসলেম ভারত পত্রিকায় এবং ১৯২১ সালে (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২৭ সালের জুন মাসে (শ্রাবণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়৷ বাঁধন হারা উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস।
বাঁধন হারা উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা মোট দশটি। একটি চরিত্র আরেকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। নুরু ও মাহবুবা একে অন্যকে পছন্দ করে এবং বিয়ের তোড়জোড়ের মাধ্যমে কাহিনির সূচনা। এই সময়ে নুরু বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। নুরুর সেনাবাহিনীতে যোগদানের পিছনে দেশ ও জাতিকে রক্ষার কোন তাগিদ ছিল না। এই উপন্যাসের আরও চরিত্র মাহবুবা, রাবেয়া ও সাহসিকা বাল্যসখী। তাদের মধ্যে পত্র যোগাযোগ হয়। সাহসিকা তার নামের মতই সাহসী ও প্রতিবাদী। চিরকুমারী সাহসিকা নারীদের ওপর অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। মাহবুবা নুরুল হুদাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু নুরুল হুদা কোনো বাঁধনে জড়াতে চায় না। অবশেষে মাহবুবার বিয়ে হয়ে যায় চল্লিশোর্ধ্ব এক জমিদারের সঙ্গে। কিছুদিন বাদেই মাহবুবা বিধবা হয়ে যায়। নুরুল হুদাকে সে লেখে যে, সে মক্কা ও মদিনায় তীর্থ ভ্রমণে যাবে এবং নুরুল হুদার কর্মস্থল বাগদাদেও যেতে পারে। নুরুল হুদা মাহবুবাকে নিষেধ করে না। তাদের দুজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনার মাধ্যমে শেষ হয় উপন্যাসটি। মৃত্যুক্ষুধা কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় উপন্যাস। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সপরিবারে মেজবউয়ের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ এ উপন্যাসকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছে! অন্যদিকে রুবি আনসারকে ভালোবাসলেও তার বাবা তাকে বিয়ে দেয় আইসিএস পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। অতঃপর মোয়াজ্জেমের মৃত্যু এবং রুবির জীবনের দুর্বিষহ চিত্র তথা নারী জীবনের বাস্তব চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। তৃতীয় উপন্যাস কুহেলিকা এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নজরুলের রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লবী স্বদেশী দলের সঙ্গে যুক্ত। তবে নারী সম্পর্কে তার মত ইতিবাচক নয়। সবমিলিয়ে রাজনীতি, মতবাদ ও আদর্শের এক কাণ্ডারী কুহেলিকা উপন্যাসটি।
তাঁর ‘বাঁধনহারা’, ‘মৃত্যুক্ষুধা’ ও ‘কুহেলিকা’ উপন্যাসত্রয় বাংলা সাহিত্যকে নবতর ছোঁয়া প্রদান করেছে। সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, আদর্শ, মতবাদের রঙে রাঙিয়ে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছেন আজও।
কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস রচনায় যেমন নতুনত্ব দেখিয়েছেন তেমনই কবিতায় তাঁর গরিমা অগাধ। তাঁকে টপকে যাওয়ার মতো প্রতিভা আজও বাংলা সাহিত্যে কেন বিশ্বসাহিত্যেও আছে কিনা সন্দেহ! কাজী নজরুল প্রেম-দ্রোহ-সাম্যের কবি। তাঁর প্রতিটি কাবিতায় মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে। মনুষ্যত্ব, বিবেক, প্রেম, দ্রোহ, সামতাই যেন নজরুলের জীবনে চরম সত্য। সেই সত্যের পথ ধরেই তিনি হেঁটেছেন। গেঁথেছেন মনের ভাষ্য। আর এই ভাষ্য শিল্প-সত্যের রূপে পাঠককে আপ্লুত করেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো যথাক্রমে: অগ্নিবীণা (১৯২২), সাম্যবাদী (১৯২৫), ঝিঙে ফুল (১৯২৬), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), মরুভাস্কর (১৯৫১(, দোলন-চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), চিত্তনামা (১৯২৫), ছায়ানট (১৯২৫), পুবের হাওয়া (১৯২৬), সর্বহারা (১৯২৬), ফণী-মনসা (১৯২৭), সঞ্চিতা (১৯২৮), জিঞ্জীর (১৯২৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয় শিখা (১৯৩০), নির্ঝর (১৯৩৯(, সঞ্চয়ন (১৯৫৫), ঝড় (১৯৬১) ও নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা (১৯৮২)।
কাজী নজরুলকে বিদ্রোহী-সাম্য ও প্রেমের কবি হিসেবেই অভিহিত করা হয়। তাঁর কবিতায় দ্রোহের যে রূপ তা দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠেছিল ব্রিটিশরাজ। তাইতো তাঁর রচনা বাজেয়াপ্তও করা হয়। তবু তিনি বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত তাইতো তাঁর সুর কখনো স্তিমিত হয়ে যায়নি। বরং আরও তেজের প্রখরতায় ডুবিয়েছেন শাসক-শোষকশ্রেণিকে। জয়গান গেয়েছেন মানুষের-মনুষ্যত্বের। তিনি বলেছেন: গাহি সাম্যের গান যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান আবার বলেছেন; গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান। সাম্যের এই কবিই আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। কবিতায় তাঁর ঝাঁঝালো কণ্ঠ পরিস্ফুট হয়েছে এভাবে; "আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস/ মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস/ আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।" একদিকে প্রেম অন্যদিকে দ্রোহ; এক হাতে গোলাপ অন্য হাতে অস্ত্র- নজরুল কাব্যে এ এক বিচিত্র-বিস্ময়।
কাজী নজরুল শুধু ঔপন্যাসিক-কবিই নয় গল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। নজরুলের গল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রেম। নিখাদ প্রেমের চিরকালীন আকুতি ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে। এই প্রেম শুধু মানসীর প্রতি নয়, দেশের প্রতিও। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ "ব্যথার দান" ১৯২২ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের গল্পগুলোর ভাষা আবেগাশ্রয়ী, বক্তব্য নরনারীর প্রেমকেন্দ্রিক। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় "রিক্তের বেদন" গল্পগ্রন্থটি। এখানে মোট আটটি গল্প স্থান পেয়েছে। এছাড়া "শিউলিমালা" (১৯৩১), হক সাহেবের হাসির গল্প, সাপুড়ে আখ্যান প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে রাক্ষুসী, পদ্ম-গোখরা, জিনের বাদশা প্রভৃতি গল্প ব্যাপক সাড়াজাগানো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাত্রা, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ, অবস্থান ও নানা দেশের মানুষজনের সঙ্গলাভ ও ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন সবমিলিয়ে নজরুলের গল্প এক অসামান্য স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব এনে দিয়েছে।
ঔপন্যাসিক-কবি-গল্পকার নজরুলই আবার নাটক রচনায় পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকগুলো যথাক্রমে: আলেয়া, মধুমালা, বিদ্যাপতি, পুতুলের বিয়ে, জাগো সুন্দর চির কিশোর, শ্রীমন্ত, বিষ্ণুপ্রিয়া, বনের বেদে, ঝিলিমিলি, সেতু–বন্ধ, ভূতের ভয় ইত্যাদি। নজরুলের ‘আলেয়া’ একটি রুপক নাটক। এ নাটকের তিনটি প্রধান নারী চরিত্র। কৃষ্ণা চিরকালের ব্যর্থ প্রেমিকা, জয়ন্তি তেজীয়ান রাণী, শক্তির প্রতীক আর চন্দ্রিকা চিরকালের কুসুম পেলব প্রাণ চঞ্চল নারী কৃষ্ণা রাজা সীনকেতুর প্রধানমন্ত্রী। নজরুল নারীকে ক্ষমতায়ন করেছেন এ নাটকে কৃষ্ণার মাধ্যমে। যুদ্ধ নয়, অস্ত্র নয়, হিংসা দ্বেষ নয়, প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়’ আলেয়া’ নাটকে। এছাড়া নজরুলের ক্ষুদ্র নাটিকা ও রেকর্ড নাট্য রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ‘পটু ও খুকু’ , কে কি হববিল, চারকালার শ্বাশুড়ি ও পুত্রবধূ, বিয়েবড়ি, বাসন্তিকা, ঈদুল ফিতর, পুরনো বলদ ও নতুন বৌ, শাল পিয়ালের বনে, ঈদ, বিলেতি ঘোড়ার বাচ্চা উল্লেখযোগ্য। ফলে অন্যান্য সাহিত্য শাখার মতো নাটক রচনায়ও তাঁর অবদান কম নয়।
নজরুলকে কোন পরিচয়ে বাঁধা যাবে সে হিসেব মেলানো দায়। তিনি আবার সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার, গীতিকার সবই। তাঁর গান-গজল-শ্যামাসঙ্গীত মন ভুলানো। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের গানের ভেতরে মিশে আছে উপমা, চিত্রকল্প, নানান দর্শন । সেইসঙ্গে সুরে সুরে পেলবতা দান করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খেয়াল, ঠুংরি ও টপ্পার সংমিশ্রণ। প্রকৃতার্থে নজরুলের আগে বাংলায় কেউ গজল গান লেখেননি। তিনিই প্রথমে বাংলা গানে গজলের সংযোজন ঘটান। গানে যেমন, গজল, শ্যামা সঙ্গীতেও তেমনই সমান পারদর্শী ভূমিকা রেখেছেন। "আমি সুন্দর নহি জানি, আধো-আধো বোল, না-ই পরিলে নোটন-খোঁপায়, অয়ি চঞ্চল-লীলায়িত দেহা, ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি, ঝরাফুল- বিছানো পথে এস, প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই, আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে, কার মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজে, নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই, বল্ রে তোরা বল্ ওরে ও আকাশ-ভার তারা, বল্ সখি বল্ ওরে সরে যেতে বল্, নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গান। এছাড়া গজল, শ্যামাসঙ্গীত রচনায়ও তিনি সমান পারদর্শী।
এছাড়া প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য রচনা করেও আলোকোজ্জ্বলভাবে সমাসীন হয়ে আছেন। তাঁর অনুদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর-খৈয়ম পাঠকমহলে আজও সাড়া জাগিয়ে চলেছে। সম্পাদনা করেছেন দৈনিক নবযুগ (১৯২০), ধূমকেতু(১৯২২), লাঙল (১৯২৫) পত্রিকা। উপন্যাস-কবিতা-গল্প-নাটক-প্রবন্ধতেই নয় সম্পাদনার মাধ্যমেও কাজী নজরুল ইসলাম বিপ্লবী ধারার সূচনা করেন। পত্রিকার শুরুতেই তিনি একটি সমতাভিত্তিক শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণের প্রশ্নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যা আজও তাঁকে স্বতন্ত্র আসনে অধিষ্ঠান রেখেছে।
কাজী নজরুল ইসলাম বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল শিল্পী। তাঁর উপন্যাস-কবিতা-গল্প-নাটক-প্রবন্ধ-সঙ্গীত-অনুবাদ-সম্পাদনা সবক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যের ভিন্নতা, শব্দের কারুকার্য, মেদহীন বর্ণনাভঙ্গি, পুরাণ-আরবি-ফারসির নিপুণ ব্যবহার তাঁর রচনাকে বিশেষভাবে শিল্পমণ্ডিত করেছে।